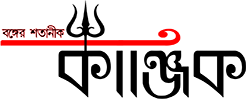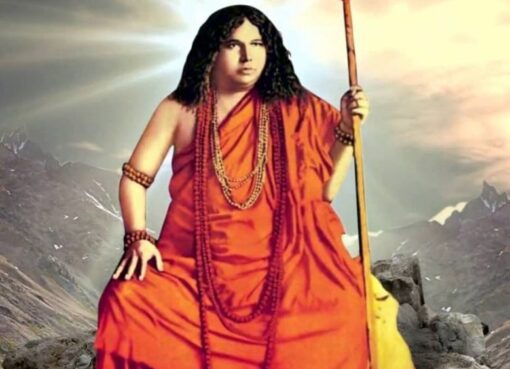-শ্রী শ্রীজিৎ দত্ত
ইতিহাস লিখতে বসেছি। কার ইতিহাস? বাঙ্গালীর ইতিহাস। কোন্ যুগের বাঙ্গালী? অগ্নিযুগের। তা এখন সব ছেড়ে হঠাৎ অগ্নিযুগের ইতিহাস ঘাঁটা কেন? বলি শুনুন।
আপনি-আমি যে সময়কালে বেঁচে আছি, অর্থাৎ এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক – এ-সময়টা বড় বিচিত্র টালমাটাল এক সময়। এই সময়কালে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের অগ্রগতি ও অধোগতি একইসঙ্গে ঘটছে। শুদ্ধমাত্র বিগত তিনটি দশকে যোগাযোগ, জীবনযাত্রার মান,প্রযুক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের নিরিখে সভ্যজগতের মানুষ যেমন চোখ-ধাঁধানো অগ্রগতি লাভ করেছে, ঠিক তেমনি মানবিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক মানব-সংস্কৃতির বিচারে সে পাল্লা দিয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছে।মনে রাখা দরকার, এই যুগপৎ অগ্রগমন ও অধঃপতনের খেলা কিন্তু ঘটমান বর্তমান কালের বিষয়, অর্থাৎ এটা এখনো ঘটে চলেছে – এবং সম্ভবতঃ আরও অনেকখানি সময় ধ’রে ঘটতে থাকবে।
এই দ্বিমুখী গতির মধ্যে যেটা সামনের দিকে চলা, সেই বস্তুবাদী অগ্রগতির কারণ সম্পর্কে আমরা সকলেই মোটামুটি অবগত আছি। এখানে মজার কথা হচ্ছে, এই শিকড় আল্গা হয়ে যাবার পিছনে সভ্য জগতের বস্তুবাদী অগ্রগতির বা উন্নতির একটা বড় ভূমিকা আছে। বাঙ্গালী তথা অধোগতির দিকে চোখ রাখব। এই অধোগতির অন্যতম বড় কারণ হ’ল পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য জাতির মানুষগুলির শিকড় আল্গা হয়ে যাওয়া। ভারতীয় জাতির ক্ষেত্রে তো বটেই, পৃথিবীর যে-কোনো সভ্য জাতির মানুষের বেলাতেই এ-কথাটা খাটে।এই মুহূর্তে যাঁদের বয়েস আট থেকে আঠাশের মধ্যে, তাঁদের একটা বড় অংশই নিজেদের শিকড় নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। শিকড়ের বোধ বস্তুতঃ ইতিহাসবোধ। কীসের ইতিহাস? নিজের পরিবার-সমাজ-দেশ তথা জগতের ইতিহাস।
এখন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হতে পারে – স্কুল-কলেজের সিলেবাসে যে ইতিহাস পড়ানো হয়ে থাকে, সেইটি মন দিয়ে পড়লেই তো ল্যাটা চুকে যায়। ল্যাটা যদি সত্যিই চুকে যেতো, তাহলে সিলেবাসের তালিকাভুক্ত টেক্সটবই রচনা-পঠন-পাঠনের বাইরে আলাদা ক’রে কেউই ইতিহাসচর্চা করবার বা ইতিহাস লেখবার প্রয়োজন বোধ করতো না – আমাদের এই যে ইতিহাস লিখতে বসেছি তারও দরকার পড়তো না। অর্থাৎ স্রেফ স্কুল-কলেজের ইতিহাসপাঠে সমস্যা মেটবার কোনো লক্ষণ অন্ততঃ এখনো অব্দি দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি আমাদের স্কুল-কলেজগুলোতে ইতিহাসের পঠন/পাঠন ঠিকমতো হচ্ছে না? উত্তরে একদল বলবেন – কই, না তো, পড়াশুনো-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা খুব হচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর-পিএইচডি বেরুচ্ছে, রাশি রাশি টেক্সটবই থিসিস ছাপা হচ্ছে, সব তোভালইচলছে। অন্য আরেকদল বলবেন – যেসব পাঠ্যবই থেকে আট থেকে আটাশ ইতিহাসের পাঠ নিচ্ছে, বিস্তর গলদ রয়ে গিয়েছে তারই মধ্যে, আর সেইসব পাঠ্যপুস্তক যাঁরা রচনা করছেন তাঁরা ব্যক্তিমানুষ তথা এই সমাজের শিকড়গুলিকে আলগা করবার সাধনায় নিমগ্ন।
সে যাই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে যে ইতিহাস-সংক্রান্ত সমস্যা শুধুমাত্র পাঠ্যবই কিংবা ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার চৌহদ্দির ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই। সে সমস্যার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দুটোই আরও গুরুতর। খেয়াল করুন,দেশে দেশে কালে কালে সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন সব ধরণের মানুষের মনে আপন সমাজ-সংস্কৃতির তথা স্বদেশের ইতিহাসবোধটি যাঁরা বংশ-পরম্পরায় অথবা শিষ্য-পরম্পরায় জাগরূক রাখতেন, সেই কথকঠাকুর/ চারণকবি/ গল্প-বলিয়েদের প্রজাতি আজকের দিনে প্রায় লুপ্ত। আমাদের দেশে পরম্পরাগত ব্যবস্থার পাশাপাশি গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যথাক্রমে নভেল, থিয়েটার ও সিনেমা জনমানসে এই স্ব-সমাজ ও স্বদেশের ইতিহাসবোধটিকে জাগিয়ে রাখবার এবং গ’ড়ে তোলবার কাজটি করতে তবু কিছুদূর সফল হয়েছিল। কিন্তু এই একবিংশ শতকে ইন্টারনেটের সর্বব্যাপী সর্বগামী উপস্থিতি মানুষের আচরণ ও মননকে এতদূর প্রভাবিত-বিবর্তিত করেছে (এবং করছে)যে, ইতিহাসের চিরাচরিত ধারক-বাহক-প্রচারকদের সান্নিধ্যে আসবার অথবা তাদের পদপ্রান্তে বসবার মতো সময় বা ধৈর্যটুকুও আজ মানুষের করায়ত্ত নয়।
ফলতঃ, জগতব্যাপী মানুষের ইতিহাসবোধ তথা তার পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয় শিকড়বোধ ক্রমশঃ আলগা হয়েই চলেছে। বাকি দুনিয়ার কথা ছেড়ে শুধু ভারতের দিকেই যদি তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষজন তো বটেই – এমনকি আজকাল পাড়াগাঁয়েও এমন ধরণের মানুষের খোঁজ আর দুর্লভ নয় যিনি শিকড়-বিচ্যুত, যারা সাংস্কৃতিকভাবে ছিন্নমূল। এমনতর মানুষের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, জীবনযাপন, ধর্ম-কর্ম সবক্ষেত্রেই সেই বিচ্যুতির লক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ফলে এ-মুহূর্তে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে শিকড়-আলগা-হয়ে-যাওয়া মানুষের ভিড়; সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটি (কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে) প্রায় উধাও। আর এ-কথা কে না জানে যে, শিকড় একবার আলগা হয়ে গেলে চারা থেকে মহীরুহ –সবই উপড়ে ফেলা সহজ হয়। এবং এইভাবে ওপড়াতে ওপড়াতে একসময় যা ছিল শ্যামল কানন, তা ধীরে ধীরে পরিণত হয় ঊষর মরুতে। তারপর হঠাৎ একদিন কোনো-একটা বিকট গোলমালের আওয়াজে চমকে জেগে উঠে আমরা দেখতে পাই যেবাংলা থেকে বালুচিস্তান, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আসমুদ্রহিমাচল সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা দেশমাতা ভারতবর্ষের উপর ঘনিয়ে এসেছে বিজাতীয় মরুসংস্কৃতির ধূসর ছায়া। আমরা আরও দেখতে পাই যে ক্রমবর্ধমান সে-ছায়ার প্রাণশোষণকারী গ্রাসে অধুনা গ্রস্ত ভারতীয় মনন বেজায় অপ্রস্তুত, আর বাঙ্গালী মনন তো একেবারেই উদ্ভ্রান্ত। ভারতে, এবং বিশেষ ক’রে আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বাংলায় গত চার-পাঁচ দশকে যে বিষয়টা বেশ ভালোরকম চোখে পড়ে তা হ’ল সংস্কৃতিগত অনুর্বরতা, প্রাণঢালা সৃষ্টিশীলতার অভাব, আর সত্যকথনে ঘোর অনীহা।
এই সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মরু-করণের অ্যান্টিডোট বা প্রতিষেধক টিকা হিসেবে যা চাই তা হ’ল ইতিহাস। বাঙ্গালীর ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। ভারত-সভ্যতার ঊষাকাল বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে মহাভারতের যুগ থেকেই বাঙ্গালীর ইতিহাসের টুকরো-টাকরা পরিচয় আমরা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত মৌখিক ইতিহাস ও তার চিরাচরিত ইতিহাস-পুরাণের মধ্যে পেয়ে থাকি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে-ইতিহাসও অনেকাংশে কুয়াশায় ঘেরা। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালীর ইতিহাসের বেশ অনেকখানিই আজ আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তা বিতর্ক অথবা প্রশ্নচিহ্ন থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেনি। তার তুলনায় বরং বাঙ্গালীর ইতিহাসের যা সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, বাঙ্গালী তার সুপ্রাচীন চলমান ইতিহাসের যে পর্বে সর্ব-অর্থেই সমগ্র ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিল, সেই ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের গোড়ার দশকগুলোর ইতিহাসের উপাদান অনেক বেশী স্পষ্টভাবে দ্বিধাহীনভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত। সুখের কথা, বাঙ্গালীর গর্বের অগ্নিযুগও তার ইতিহাসের এই পর্বেরই অন্তর্গত।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অগ্নিযুগের ইতিহাস লিখতে বসলে সে-ইতিহাস আখ্যান আরম্ভ করবো কোথা থেকে? ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে? নাকি তার কয়েকবছর আগে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার কাল থেকে? নাকি সমিতির বীর বিপ্লবী-যুগল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীর মেদিনীপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা! স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো মনে আসে।
উত্তরে বলবো, না –বাঙ্গালীর অগ্নিযুগের অথবা অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর চরিত্রটিকে যদি বুঝতে হয়, যদি অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর ইতিহাসের সুলুকসন্ধান করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে সময়ের নিরিখে বেশ খানিকটা পিছিয়ে যেতে হবে। পৌঁছে যেতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দশকগুলোতে। সেই সময় থেকে আরম্ভ ক’রে, কালের গতি অনুসরণ ক’রে রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, আনন্দমোহন বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ, ওকাকুরা, নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক বিনয় সরকার, আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, আচার্য যদুনাথ সরকারের মতো একঝাঁক চরিত্রের বিচিত্র বহুমুখী কর্মকাণ্ড এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলির উপর এঁদের সুদূরপ্রসারী –অথচ অনেকাংশে অকথিত – প্রভাবকে নিবিষ্ট মনে পাঠ করতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনে, শরীরে এবং আত্মায় যেসব বিপ্লব ঘ’টে গিয়েছিল সেগুলো ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে হ’লে এই চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে গোড়ায় একটা মোটামুটি ধারণা থাকা চাই। সে ধারণাটি তৈরি করতে পারলে তবেই একমাত্র আমরা অগ্নিযুগের অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, এবং সর্বোপরি অগ্নিযুগের নির্যাস ও চরম পরিণতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লব চেষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারবো, নচেৎ নয়। কাজেই অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর ইতিহাসকে বুঝতে চাইলে ১৯০২ কিংবা ১৯০৫ থেকে পাঠ শুরু করলে হবে না, কারণ সে-ধরণের পাঠে অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর ইতিহাস এবং সে ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের বোধ ও ধারণা রয়ে যাবে অসম্পূর্ণ – এমনকি ভ্রান্ত।
(ক্রমশঃ)
(লেখক পরিচিতি – শ্রী শ্রীজিৎ দত্ত একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কবি, নাট্যকার, অনুবাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ)