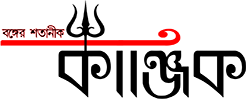-শ্রী শ্রীজিৎ দত্ত
সমিধ সংগ্রহ – বিপ্লবের প্রস্তুতি
আগের পর্বে লিখেছিলাম, “বাঙ্গালী” র অগ্নিযুগের অথবা অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর চরিত্রটিকে যদি বুঝতে হয়, যদি অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর ইতিহাসের সুলুকসন্ধান করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে সময়ের নিরিখে বেশ খানিকটা পিছিয়ে যেতে হবে। পৌঁছে যেতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দশকগুলোতে।” একথা বলবার মুখ্য কারণ হলেন রাজা রামমোহন রায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে আমরা ‘সমাজ-সংস্কারক’ তকমা দিয়ে দায় সারি, তাই তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও চরিত্রের বারো আনাই থেকে যায় অজানা। অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখতে ব’সে রাজা রামমোহনকে নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে দেখে অনেকেই তাই ভ্রুকুঞ্চন করবেন। তেমনটা করা অনর্থক। অগ্নিযুগের বাঙ্গালীর বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল, তার মালমশলার জোগান দিয়েছেন রাজা রামমোহন। ব্যাপারটা খোলসা ক’রে বলি।
শ্রী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬ – ১৯৭৬) ছিলেন অগ্নিযুগের একজন সুপরিচিত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী নেতা। যুবক বয়সে তিনি বাঙ্গালী বিপ্লবীদের আদি আখড়া অনুশীলন সমিতির সদস্য হন, যা অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উৎসস্থল ছিল। কিংবদন্তি বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীনের (অর্থাৎ শ্রী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ঘনিষ্ঠ সহযোগী যাদুগোপাল ‘বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি’ নামে একটি স্মৃতিকথা লিখেছেন। এই স্মৃতিকথায় অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ঘটনাবলীকেএকেবারে ভিতর থেকে প্রত্যক্ষ করা যাদুগোপাল বিপ্লবের ধারণা নিয়ে বেশ কিছু অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের একটা রূপরেখা এঁকে দিয়েছেন, এবং অগ্নিযুগের উত্থানের পিছনে যে গভীর সাংস্কৃতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কারণগুলি রয়েছে সেগুলি নির্দেশ করেছেন।
যাদুগোপাল প্রশ্ন তুলেছেন : “বিপ্লব বলতে কি বুঝি?” প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন – এবং সে উত্তর বিপ্লবকে কোনো এক অনিয়ন্ত্রিত, অন্ধ শক্তির প্রকাশ কিংবা বিস্ফোরণ ব’লে মনে করা দৃষ্টিভঙ্গিটিকে সোজাসুজি অস্বীকার করে। তৎপরিবর্তে, বিপ্লবের একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য বা নকশা আছে ব’লে যাদুগোপাল মনে করেন। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের প্রতিধ্বনি ক’রে যাদুগোপাল বিপ্লবকে মানুষের সামাজিক-ঐতিহাসিক অগ্রগতির একটি আবশ্যিক উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা কিনা দু’টি পরস্পরবিরোধী অথচ পরস্পর-সংযুক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। যাদুগোপাল বলছেন, এই উপাদানগুলির একটি হ’ল যে কোনো সমাজের ইতিহাসের কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ের স্থিতাবস্থা; এবং অন্যটি হচ্ছে দৃশ্যমান জগতের সদা পরিবর্তনশীল ঘটনাবহুল চরিত্র। এই দ্বিতীয় উপাদানটিকে তিনি সংস্কৃত পারিভাষিকে ‘সংসার’ ব’লে অভিহিত করেছেন,যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে “যা চলমান বা সরে সরে যাচ্ছে” অর্থাৎ যা নিয়ত পরিবর্তনশীল – ক্রমাগত রূপান্তরিত হতে থাকাই যার চরিত্র। প্রথম উপাদানটিকে যাদুগোপাল বাংলায় ‘বাদ’ এবং দ্বিতীয়টিকে ‘বিসম্বাদ’ নামে ডেকেছেন – যা আমাদেরকে স্মরণ করায় হেগেলের ‘থিসিস’ এবং ‘অ্যান্টিথিসিস’ এর দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে।
এরপর যাদুগোপাল দাবী করেছেন যে ‘বাদ’ ও ‘বিসম্বাদ’ অভিধেয় এই দুই উপাদানের মধ্যেকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং সংঘর্ষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক অগ্রগতির জনক। কিন্তু সবরকম অগ্রগতিই শেষ পর্যন্ত একটি বিশ্রামস্থল বা একধরণের স্থিতিশীল পরিস্থিতি বা স্থিতাবস্থায় পৌঁছোতে চায়। যাদুগোপাল আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই প্রকারের স্থিতাবস্থা নেহাতই আপেক্ষিক, কারণ তা অস্থায়ী। তবু এটিকে এক ধরণের সংশ্লেষ বলা যেতে পারে (যাদুগোপালের ভাষায় ‘সম্বাদ’), যা আসলে এই ‘বাদ’ ও ‘বিসম্বাদ’-এর মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া তথা সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত একটি ভারসাম্যের অবস্থা। যথাসময়ে এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তার প্রাথমিক ফল – যেমন, মানুষের হাতে-গড়াকোনো একটি সংগঠন –লোপ পেয়ে যায়। এবং তারপর উঠে আসে আরেকটি দল, আরেকটি সংগঠন, যা অধুনালুপ্ত পূর্বসূরির থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে এবং যা পূর্বসূরির চরিত্র হতে রূপান্তরিত ও ভিন্ন চরিত্রের এক নূতন শক্তি-প্রক্রিয়া বা আন্দোলনকে মূর্ত ক’রে তোলে। তারপর যথাসময়ে আপন ফল প্রসব করবার পর এইনূতন বা রূপান্তরিত সংগঠনটিও লুপ্ত হয়। সমাজে এভাবেই বিপ্লবের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে।
যাদুগোপাল মনে করেন, এই হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দেখা, বোঝা, ও ব্যাখ্যা করা কর্তব্য। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি যে আমাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু যাদুগোপাল এই তত্ত্বের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা বাঙ্গালীর অগ্নিযুগের ইতিহাস-জিজ্ঞাসুদের জন্যে বেশ উপাদেয়। প্রথমত, তিনি অনুশীলন সমিতিকে বাংলার একমাত্র বহুধাবিস্তৃত বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা ১৯০৩ সাল থেকে কলকাতাকে প্রধান ঘাঁটি ক’রে দ্রুত সমগ্র অবিভক্ত বঙ্গে বিস্তার লাভ করে। কিছুকাল বাদে এই সংগঠন তার গতি হারালে পর ‘যুগান্তর’ পত্রিকা পরিচালনকারী গোষ্ঠীকে ঘিরে আরেকটি নামহীন বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী সংগঠন গ’ড়ে ওঠে। আবার এক সময়ে সেই নতুন সংগঠনটিও লোপ পায়। তারপর উঠে আসে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় অনুশীলন সমিতির বিখ্যাত কেন্দ্র।
ঐ একই সময়ে গোটা বঙ্গদেশ জুড়ে এবং বঙ্গের বাইরেও আরেকটি নামহীন সংগঠন গজিয়ে ওঠে। সময়ের সাথে সাথে এই নতুন এবং নামহীন বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী সংগঠনটি ‘যুগান্তর’ নামে পরিচিত হয় – যা দ্রুত সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করে। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে, এবং বিশ শতকের বিশ্বব্যাপী প্রভাব-সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলির পর্দা উন্মোচিত হওয়ার সাথে সাথে এই দুই সংগঠন ক্রমে একটি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম দেয়। তবে। যাদুগোপালের মতে, মার্কসবাদ কেবলমাত্র খাওয়া-পরার সম্পর্কিত কয়েকটি বুনিয়াদি সমস্যার সমাধান বাৎলাতে পেরেছিল। কিন্তু ঐসব বুনিয়াদি অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হওয়ার পরেও অন্য যেসব বুনিয়াদি চাহিদা রয়ে যায় সেগুলির কী হবে? এই প্রসঙ্গে যাদুগোপাল মানুষের আত্মার বুনিয়াদি চাহিদাগুলির কথা উত্থাপন করেন; বলেন সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা, মানুষের মননের তথা আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনেরকথা। এ-কথা আলোচনার প্রসঙ্গেই যাদুগোপাল একটি নতুন সংশ্লেষ-মূলক দর্শনের দিকে ইঙ্গিত করেন, যার মধ্যে বিবেকানন্দ স্বামীর প্রচারিত জীবসেবা-দর্শনের জোরালো প্রতিধ্বনি মেলে।
ভারতে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ইতিহাস এবং তার গভীর সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণগুলি খতিয়ে দেখার ব্যাপারে আমরা যাদুগোপালের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির সাথে একমত হই বা না-হই, এই ইতিহাসকে বোঝার ক্ষেত্রে যাদুগোপাল আমাদের জন্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র রেখে গিয়েছেন। সে-সূত্রটি মানবাত্মার আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্রান্ত, যা কিনা অগ্রগতি তথা স্বাধীনতা লাভের জন্য মানুষের যাবতীয় চেষ্টা ও সংগ্রামের পরম ভিত্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে। আমার রচনায় আমি এই সূত্রটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করবো, কিন্তু আমার পদ্ধতিটি হবে যাদুগোপালের পদ্ধতির ঠিক বিপরীত :আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন ক’রে এই ইতিহাস লিখছি, সেই পদ্ধতিতে মানবাত্মার আধ্যাত্মিক পিপাসাগুলি চরিতার্থ করবার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে বিশেষভাবে খতিয়ে আলোচনা করা হবে, যাতে বোঝা যায় যে কীভাবে এইসমস্ত উপাদান মানুষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে (এমনকি বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টাগুলিকেও) শুধুমাত্র যে উস্কে দিয়েছে তাই নয় বরং সেগুলিকে চরিতার্থ করতেও সাহায্য করেছে।
এই সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও আলোচনা আমি করবো সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটে, এবং বিশেষ করে অগ্নিযুগের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। মানুষের অন্যান্য যাবতীয় বিচরণক্ষেত্রের কর্মপ্রচেষ্টাকে মানবাত্মার মৌলিক চাহিদাগুলির জনক হিসেবে বিবেচনা করা – যেমনটা যাদুগোপাল করেছেন, তেমনটা না ক’রে আমি দেখাতে চেষ্টা করবো কীভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় প্রচেষ্টাই মুখ্যত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশের পথটিকে নির্মাণ করেছে – এবং বিশেষ ক’রে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের রাজনীতির পথকে তা পুষ্ট করেছে।
সত্যি বলতে, ভারতে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ও তার ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির গুরুত্ব যাদুগোপাল নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় যাদুগোপাল সরাসরি উপনিষদের যুগে ফিরে যান, যাতে তিনি বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের অগ্নি প্রজ্বলন করতে সাহায্য করা উপাদানগুলির – অর্থাৎ অগ্নিযুগের ‘সমিধ’-এর – মূল উৎসটি নির্ধারণ করতে পারেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের সেই ঊষালগ্ন থেকে আরম্ভ ক’রে তারপর তিনি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের পরবর্তী যুগ অথবা সময়কালগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন – যেমন বুদ্ধদেব এবং তাঁর ধর্মের সঙ্ঘস্থাপন, বিভিন্ন জনপদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, মৌর্যদের সুমহান সাম্রাজ্য, চাণক্য কর্তৃক অখণ্ড ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্যসাধন ও সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অধীনে ‘এক জাতি, এক পতাকা’-র জাতীয়তাবাদী ধারণাটির প্রবর্তন, চার্বাক এবং লোকায়তদের তর্কবাদিতা এবং বস্তুবাদ, এবং মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যুগের প্রাক্কালে ভারতের বীর রাজপুত, মারাঠা এবং শিখদের ইতিহাস।
একটি সপাট-সামগ্রিক ঐতিহাসিক রূপরেখা চুম্বকাকারে তুলে ধ’রে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী লেখক শ্রী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাসের এই বিচিত্র পর্বগুলিরপরিক্রমা করেছেন –যাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি,রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক গৌরব ভারতীয় বিপ্লবীদের চিন্তায় এবং কর্মে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এ-কথা বিপ্লবী যাদুগোপাল তাঁর স্মৃতিচারণায় নিজেই স্বীকার করেছেন।
(ক্রমশঃ)
(লেখক পরিচিতি – শ্রী শ্রীজিৎ দত্ত একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কবি, নাট্যকার, অনুবাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ)