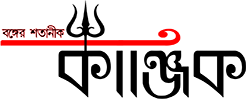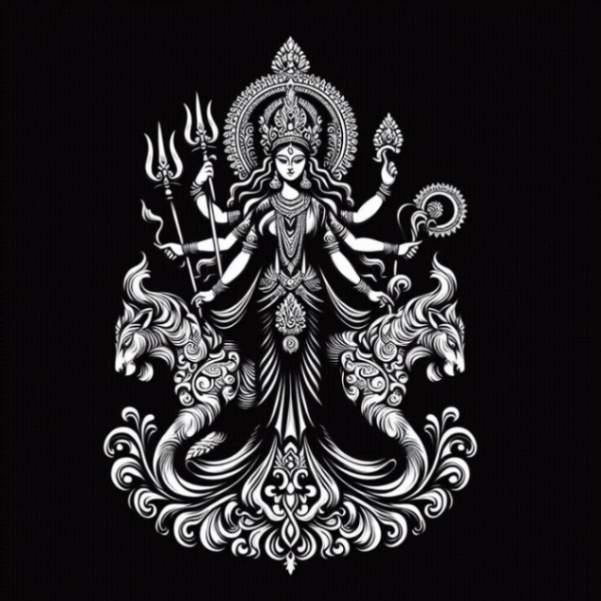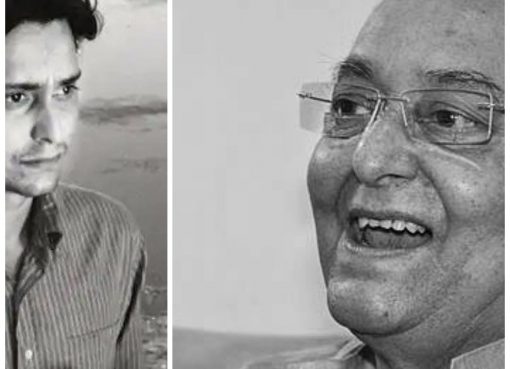– শ্রী শ্রীজিৎ দত্ত
আজকের দিনে বঙ্কিমের প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কোথায়? যেহেতু একজন সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রাসঙ্গিকতা বিভিন্ন যুগের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সমালোচকের বিচার্য হয়ে থাকেন, তাই স্বাভাবিকভাবে বঙ্কিম তথা বঙ্কিমী সাহিত্য ও সমালোচনার এই যুগধর্মী দৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যাত হবেন। কিন্তু তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মকে শুদ্ধমাত্র খণ্ড-খণ্ড ভাবে সমসময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করলে সে বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। এর কারণ, বঙ্কিম কেবল সাহিত্য পিপাসু জনতার চিত্তরঞ্জন করবার উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, বরং আমরা দেখতে পাই যে, তিনি সাহিত্যসেবাকে দেশসেবার পন্থা হিসেবে প্রয়োগ করছেন, এবং উপরন্তু বয়োকনিষ্ঠ সাহিত্যিকদেরকে ঐ পথে দেশ তথা মনুষ্যসমাজের সেবা করতে সরাসরি প্রণোদিত করছেন : “যদি মনেএমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। …যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।” (“বিবিধপ্রবন্ধ”, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৬, পরিষৎ-সংস্করণ)
এর ফলে সমালোচনার যে বিশিষ্ট দিগন্তটি উন্মোচিত হয়েছে, তা হ’ল ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বঙ্কিম ও বঙ্কিমী সাহিত্যের বিচার। এইখানে স্পষ্ট ক’রে বলা দরকার যে, এই ইতিহাস শুধুমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস নয় – এখানে ইতিহাস বলতে যা বোঝাতে চাইছি তা হ’ল প্রবহমান ভারতেতিহাস। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ‘প্রবহমান ভারতেতিহাস’ আবার কী বস্তু? উত্তরে বলা যায়, ভারতবর্ষে (অর্থাৎ যে ভূখণ্ডকে ইংরেজরা একদা ‘ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট’ নামে ডেকেছিলেন) মনুষ্য সভ্যতার ঊষাকাল হ’তে সংস্কৃতি-মনন-ধর্মনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতির যে নিরন্তর ধারা বয়ে চলেছে, সেই নিয়ত পরিবর্তন/আবর্তনশীল ধারার অন্তরঙ্গ আলেখ্যই প্রবহমান ভারতেতিহাস। এখানে ‘অন্তরঙ্গ’ শব্দে ধরতে চাইছি নৃতত্ত্বের ‘এমিক’ দৃষ্টিভঙ্গির ধারনাটিকে। সেই হিসেবে নৃতত্ত্বের ‘এটিক’ ধারণাটিকে বলা চলে ‘বহিরঙ্গ’। এখন কথা হচ্ছে, ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সদ্য-বিকাশোন্মুখ বাংলা গদ্য সাহিত্যকে ঐ শতক ফুরোবার আগেই আধুনিক কালের উপযোগী ক’রে গ’ড়ে দিয়েছেন যে সাহিত্যিক, সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে খামোকা ভারতবর্ষে মনুষ্য সভ্যতার পঞ্চ সহস্রাব্দ-ব্যাপী প্রেক্ষাপটে ফেলে বিচার করতে হবে কেন? করতে হবে, কারণ বঙ্কিম স্বয়ং সেই প্রবহমান ইতিহাসের ধারাটির সঙ্গে – অথবা বলা ভালো সেই ধারার মধ্যে – স্বকৃত সাহিত্যকৃতিকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই শেষ বক্তব্যটিকে তলিয়ে বোঝা যাক্।
ইংরেজি উপন্যাস রাজমোহন্’স্ ওয়াইফ–এর মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের যাত্রারম্ভ। এক্ষেত্রে বঙ্কিম কতকটা তাঁর পূর্বসূরি কবিবর মধুসূদন দত্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন বলা যেতে পারে। বিজেতা অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসকের ভাষাকে করায়ত্ত ক’রে তাতে উচ্চমানের সাহিত্যসৃষ্টির উচ্চাকাঙ্ক্ষা নবীন বঙ্কিমের সমসাময়িক বাংলাদেশে অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবকই মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু মধুসূদনের মতোই বঙ্কিমের ‘পরধন’-এর মোহ কেটে গিয়েছিল – এবং তা দ্রুতই কেটেছিল। এই মোহমুক্তি ত্বরান্বিত হবার পেছনে প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের স্নাতক বঙ্কিমের সরকারী চাকরীর বছরগুলোর অভিজ্ঞতা। এই সুবাদে বঙ্কিম অবিভক্ত বাংলার অন্ততঃ বারোটি জেলায় এবং উড়িষ্যাতেও সময় কাটিয়েছেন – কখনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনো ডেপুটি কালেক্টর, আবার কখনো বা বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে। এর ফলে বঙ্কিমএদেশের একটা বড় অংশের মানুষের – বিশেষতঃ কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, অভাব-আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে ভূয়োদর্শী অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞা নঅর্জন করতে সক্ষম হন। একে তো ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী, তদুপরি কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল বাংলা তথা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে মানুষের জীবন কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়ে তাঁর চোখ খুলে গিয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষের প্রবহমান ইতিহাসকে এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আপন হৃদয়ে সম্যকভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন, যা তাঁর ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিলব্ধ বিদ্যাকে পূর্ণতরএবংসার্থক ক’রে তুলেছিল। তিনি দেশের জীবনের মূল সুরটিকে ঠিকঠিক ধরতে পেরে, সেই সুরকে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করবার ব্রত গ্রহণ করেন। আর এরই মাধ্যমে তিনি আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পদ দেশবাসীর অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন অংশটির মধ্যে ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নেন।
এই উদ্যোগের একটি বড় দিক ছিল বিজ্ঞানের ধারণা ও বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার। পশ্চিমী ফিলজফির আলোকপ্রাপ্ত ও পশ্চিমী মননের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত বঙ্কিম পাশ্চাত্যের সারভাগ গ্রহণ ক’রে অসার বস্তুকে ত্যাগ করবার ক্ষমতা রাখতেন। এই সার-অসার বিচার ক্ষমতা তাঁর পূর্বসূরী বঙ্গীয় মনীষীদের মধ্যে বিশেষভাবে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বভাবে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যের মূলে যে রয়েছে বিজ্ঞান তথাপ্রযুক্তির অসামান্য উন্নতি, সে কথা উপলব্ধি ক’রে বঙ্কিম তাঁর মনন-সাহিত্যে স্পষ্ট ভাষায় ভারতবাসীকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির চর্চায় যত্নবান হবার উপদেশ দিলেন। তাঁর ভাষায় – “বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস; যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানকে অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু।…বিজ্ঞান মহায়সশকটে বাহনে, তড়িৎ-তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারত ভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিনদিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।” (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৭৯, পৃঃ ২৩৫)
লক্ষ্যণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানকে ও ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন। তিনি ‘স্বদেশী বিজ্ঞান’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা এখানে আমাদের অনুধাবন করবার প্রয়োজন আছে।
ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বলা চলে যে, বঙ্কিম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই যে ‘স্বদেশী বিজ্ঞান’ নামক ধারণাটির অবতারণা করেছেন, সেটি বাস্তবায়িত হ’তে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে আরো কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগত হবার বারো বছরের মধ্যে বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, এবং সে আন্দোলন নেহাত রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিল্পকলা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ব্যবসায়-উদ্যোগ, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনচিন্তা প্রভৃতি দেশবাসীর জীবনের নানান দিকে ছড়িয়ে পরে এবং নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ বিজ্ঞান সাধকদের মধ্যে স্বদেশী বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনা আমরা স্বদেশী আন্দোলন ও তৎপরবর্তী বছরগুলিতেই দেখতে পাই।
বিজ্ঞান হতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পদার্পণ এবং প্রযুক্তি থেকে ব্যবসায়িক উদ্যোগ – এই স্বাভাবিক বিবর্তন বঙ্গদেশে বিংশ শতকের গোড়ায় আমরা দেখেছি স্বদেশী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী বিজ্ঞানসাধক-প্রযুক্তিবিদ তথা উদ্যোগপতিদের কর্মকাণ্ডে। এ-প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বেঙ্গল কেমিক্যালের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে। বঙ্কিমের ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণা এই কর্মকাণ্ডের গোড়াকে সিঞ্চিত করেছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। বিজ্ঞানকে স্বদেশীয় আঙ্গিকে পরিবেশন করবার, সাধারণ্যের মধ্যে জনপ্রিয় করবার এই বঙ্কিমী উদ্যোগ তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ‘বিজ্ঞানরহস্য’ প্রবন্ধ সংগ্রহে এরই নিদর্শন পাই। সৌরবিজ্ঞান হ’তে নৃতত্ত্ববিদ্যা, জীববিদ্যা হ’তে মহাকাশ-পর্য্যটন, গতিবিদ্যা হ’তে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ – কী নেই সেখানে? বঙ্কিমের সমকালের নিরিখে বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সর্বশেষ গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে পাঠকবর্গের মধ্যে বিতরণ করে তিনি বিজ্ঞানকে শুধু জনপ্রিয়ই করেননি, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম ক’রে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বঙ্গীয় পরিভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে বঙ্কিমের অবদান আজকের দিনে বহুচর্চিত না হ’লেও অনস্বীকার্য। তিনি বাঙালীর মনন ও কল্পনাকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির রাজপ্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে এনে দিয়েছেন।
কর্ম-জীবনে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাবার আরেকটি ফল হয়েছিল অর্থনীতি বিষয়ে বঙ্কিমের মৌলিক চিন্তা ও মরমী ভাষায় সে চিন্তার প্রকাশ। বঙ্কিম-প্রতিভার এ-দিকটি বিশেষ ক’রে দেখতে পাই ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে। একইভাবে, বঙ্গভাষায় ইতিহাসচেতনার অনুশীলন এবং তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও বঙ্কিম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন দেখতে পাই। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস – এই দুই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ক্ষেত্রে বঙ্কিম অভূতপূর্ব অনুসন্ধিৎসা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য – “মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত বঙ্গদর্শনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ সাধারণতঃ দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে – “ভারত-কলঙ্ক বা বাঙ্গালার কলঙ্ক” এবং “বাঙ্গালীর উৎপত্তি”।
তখনও বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস-রচনায় আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। যাঁহারা ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ইতিহাস রচনা করিতেন, তাঁহারা তখনও এই প্রণালীর নাম পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।…এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর শতশত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন উক্তির মতন বলিয়া যান নাই; এখন আমরা যেমন করিয়াঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সারসত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমনই করিয়া সেই রূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।” এহবাহ্য।
এবারে দেখা যাক বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সভ্যতার স্বকীয় আলোকের সম্মুখে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধার-করা আলোকে আলোকিত আধুনিক ভারতবর্ষকে দাঁড় করিয়েছেন, এবং তার মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রবহমান ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের মধ্যে সমন্ব য়স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমার মতে, এইটি বঙ্কিমচন্দ্রের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান; এবং এই অবদান তিনি রেখে গেছেন ‘কৃষ্ণচরিত্র’, ‘ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন)’, ‘আনন্দমঠ’, ‘রাজসিংহ’, ‘দেবীচৌধুরানী’, ও ‘সীতারাম’ – এই কয়টি রচনার মাধ্যমে। কীভাবে তিনি এই সমন্বয় সাধন করলেন? বৈদিক যুগে সংহিতার মাধ্যমে যে জীবনাদর্শ ভারতীয় সমাজে প্রচারিত হয়েছিল, তা ইতিহাস-পুরাণের যুগে যুগোপযোগী সুসংহত আকারে পরিবেশিত হয়ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা মহর্ষি ব্যাস প্রোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপে। মধ্যযুগে এই জীবনাদর্শ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নানান ভাষায় পুনঃপ্রচার করেছেন রামানুজাচার্য, গুরু নানকদেব, নামদেব, রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য।
বঙ্কিম ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার অশ্বমেধের মধ্যে আরও একবার ভারতবর্ষে সেই ঋষিদ্রষ্ট সনাতন জীবনাদর্শের সত্যকে আধুনিক যুগের উপযোগী ভাব ও ভাষায় – এবং সর্বোপরি আধুনিক সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে – অনুশীলন তত্ত্ব নামে বাঙালীর মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করেছেন। এই কারণে বঙ্কিমকে সমন্বয়কারী বলব – তিনি পুরাতন ও নবীনের মধ্যে সনাতন জীবনাদর্শের সূত্রটি রক্ষা করেছেন।
বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যাক্।
একদিকে মুঘল যুগের শেষ দিকে সুবে বাংলায় পরপর নবাব আলিবর্দি খাঁ, নবাব সিরাজুদ্দৌলা, নবাব মীরজাফর এবং নায়েব নাজিম সৈয়দমহম্মদ রেজা খাঁর স্বৈরাচার ও অরাজকতায়, এবং অন্যদিকে প্রথমে রবার্ট ক্লাইভ ও তারপর ওয়ারেন হেস্টিংস পরিচালিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর-আদায় সর্বস্ব শাসনের দ্বিমুখী শোষণ-নিপীড়নে বঙ্গদেশের ভয়ানক দুর্দশা হয়েছিল; যার চরম পরিণতি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের মহা দুর্ভিক্ষ)। এই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘ’টে যায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এরপর, এই ঘটনার এক শতাব্দী বাদে আবারও এমন এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারতে দেখা দেয়, যা ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে স্বদেশীআন্দোলন ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের পথ প্রস্তুত করতে থাকে। ১৮৭৮-এর অস্ত্র আইন, সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা জারি, ইত্যাদি নানান ঘটনায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনা-অপমান এবং সেই থেকে তৈরি হওয়া অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধিপেতে থাকে। এ জিনিস চরমে পৌঁছয় ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে।
বাঙালী ততদিনে দেশকে মা ব’লে চিনতে এবং মাতৃরূপে উপাসনা করতে শিখেছে (এবং তা শিখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রই)। ফলে এই সমাজের পক্ষে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কেবল আত্ম-অবমাননাই নয়, উপরন্তু হয়ে দাঁড়াল মাতৃ-অবমাননা তথা ধর্ম-অবমাননা। বাঙালীর এতদিনকার পুঞ্জীভূত অপমান ও ক্ষোভ এবারে ফেটে পড়ল একেবারে নতুন রূপে – সংগঠিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের পথে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেই আন্দোলনের একটি বলিষ্ঠ ধারা সংগঠিত সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হ’ল। সেবারে অপমানিত-পদদলিত-বহুধা বিভক্ত এবং আপাতদৃষ্টিতে হীনবীর্য অসহায় বাঙালি সমাজের দেহে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। এগুলির মধ্যে প্রধান হ’ল ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, রাজসিংহ, সীতারাম, দেবীচৌধুরানী, এবংঅবশ্যই আনন্দমঠ। এই রচনাগুলি মুখ্য হলেও বঙ্কিমের বেশ কিছু অন্যান্য রচনাও এই ব্যাপারে গৌণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় কমলাকান্তের দপ্তর এবং দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধমূলক রচনাগুলিতে ধর্মের যে তাত্ত্বিক দিকগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলিকেই সাহিত্যরসের প্রয়োগে সজীব ক’রে তুলেছেন তাঁর তিনটি উপন্যাসে। একথা প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ যোগেশচন্দ্রবাগল ও সাহিত্যিক-সম্পাদক (এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যা য়দুজনেইউল্লেখকরেছেন।
যোগেশচন্দ্রের মতে, “‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরানী’ ও ‘সীতারাম’-এ বঙ্কিমচন্দ্র শুধু দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান নাই, কিরূপ অনুশীলন দ্বারা স্বদেশের মুক্তি সাধন সম্ভব তাহার সন্ধান দেশবাসীকে তিনি এগুলির মাধ্যমে দিয়াগিয়াছেন। এ তিনেরই উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেনঃ এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। ‘আনন্দমঠে’ সমষ্টি বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ‘দেবী চৌধুরানী’তে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; ‘সীতারামে’ সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা state বা স্বতন্ত্রশাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্যায় দেখাইয়াছেন।”
সনাতনধর্ম –অথবা ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের সূত্রপাত থেকে শুরু ক’রে একেবারে আজকের যুগ অব্দি যাকে হিন্দুধর্ম বলা হয় –সেই ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন আঙ্গিকে তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপনা করেছেন সাহিত্যসম্রাট এবং ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হিন্দুধর্মের এই নব আঙ্গিকই হচ্ছে ‘অনুশীলন তত্ত্ব’। এ নাম বঙ্কিমচন্দ্রেরই দেওয়া, এবং তত্ত্বগত বা থিওরেটিকাল দিক থেকে এটিকে একটি শক্ত ভিতের উপর তিনি দাঁড় করিয়ে গেছেন মূলতঃ তিনটি রচনার মাধ্যমে। এই তিনটি রচনা হচ্ছে‘ধর্মতত্ত্ব’, ‘কৃষ্ণচরিত্র’, এবং‘আনন্দমঠ’। এদের মধ্যে‘ ‘ধর্মতত্ত্ব’ই সর্বপ্রধান। তারপর অনুশীলন তত্ত্বের আলোচনায় যে রচনাটির নাম করা যায় সেটি হচ্ছে ‘কৃষ্ণচরিত্র’, এবং সবশেষে বঙ্কিমের কালজয়ী উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’কে বলা যেতে পারে অনুশীলন তত্ত্বের প্রায় একটি মহাকাব্যিক প্রয়োগ।
(লেখক পরিচিতি – শ্রী শ্রীজিৎ দত্ত একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কবি, নাট্যকার, অনুবাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ)