(পূর্বের সংখ্যার পর)
– বিশাখদত্ত
গান্ধর্বসঙ্গীত আলাপের স্রোতমুখ খুলেই গত পর্বের লেখাটির ইতি টেনেছিলাম।
এই পর্বে গান্ধর্বসঙ্গীতকে সাধ্যমত আরেকটু বিস্তৃত করার চেষ্টা করছি। গান্ধর্বসঙ্গীতের কালনির্ণয় করতে গিয়ে একে বৈদিকযুগের সমসাময়িক লোকপ্রিয় সঙ্গীত ধারা বলা হয়েছে এবং যা অধুনাতন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ধারার পূর্ব-প্রাকৃত-রূপও বলা যায় কিছুটা। সে দিকটায় আলোকপাত করেছি। বৈদিক সঙ্গীত মূলরূপে বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের সাথে আনুষ্ঠানিক সংযোগপূর্ণ ছিল। বলা যেতে পারে এটা কিছুটা ঔপচারিক সঙ্গীত সে অর্থে। গান্ধর্বসঙ্গীত উদ্ভূত ও প্রসারিত হয়েছে লোকরঞ্জনের নিমিত্ত, বিনোদন রূপে ও গ্রাহ্য হয়েছে সর্বজনের শিল্পকলা রূপে। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী এই সঙ্গীত নাটকের জন্য তৈরি হয়েছে। শুরুর প্রাথমিক অবস্থায় গান্ধর্বসঙ্গীত যে বৈদিক-সঙ্গীতের কুলীন সমাজে ঠাঁই পায়নি তা জানা যায়।
একে অনার্য জাতির শিল্প হিসেবে ব্রাত্য করা হয়েছিল। ভারতীয় দর্শনের ভূমিতে আমরা দেখি – যখন কোন নতুন আস্তিক দর্শন {বেদবাদী (Orthodox)} আবির্ভূত হয়েছে, সেই দর্শন নিজের অস্তিত্বকে বেদের প্রামাণ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দুর্বার চেষ্টা করেছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি একই কর্মটি করেছিলেন নাট্যশাস্ত্র তৎ-সম্ভূত গান্ধর্বসঙ্গীতকে বৈদিক কৌলীন্য এনে দিতে। চতুর্বেদের নানাস্থান থেকে উপাত্ত (Reference) যোগাড় করে ভরতমুনি তার কলাকে ‘নাট্যবেদ’ আখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই ‘নাট্যবেদ’ তত্ত্ব কতটা গ্রণযোগ্যতা পায় বৈদিক সঙ্গীত সমাজে জানি না, তবে ভরত মুনি যে বেদ-প্রামাণ্যতাকে ভিত্তি করেছেন তা স্বীকৃতি পায়। মানা হয় সামগান উদ্গত পবিত্র বীণা থেকে আর গান্ধর্ব গান এসেছে বেণুর সুরে। এই কথার মধ্যেও বীণার কৌলীন্য বেণুকে যেন ছাপিয়ে যায়। বেণু লোকসঙ্গীতের প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে যেন মনে হল- ঋক-সাম-মন্দ্রিত বীণাবাদিনীর ধ্যানকল্পনার লোক ছাড়িয়ে আমরা এই মর্ত্যের কোন গোপালক রাখালের বেণুবাদনে যুগ যুগ মোহিত হবার যাত্রাধ্বনি দেখতে পাচ্ছি এর মাঝে!
বেদ পরবর্তী রামায়ণ-মহাভারতাদি পৌরাণিক যুগের গীতি-নৃত্যকলা গান্ধর্বসঙ্গীতের পথনির্দেশ দেয়। খ্রীষ্ঠপূর্ব ৪০০-৫০০ সন গান্ধর্বসঙ্গীতের সর্বোত্তম উৎকর্ষের কাল। তখন ভারতবর্ষের নানা দেশে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় এই ধারা ব্যাপক লোকপ্রিয় হয় ও সর্বজনের সঙ্গীতকলারূপে বিস্তৃতি লাভ করে দ্রুত। রাজ-সভাগৃহের সীমা ছাড়িয়ে এই সঙ্গীত রাজ-অন্তঃপুরেও অবাধ প্রবেশাধিকার পায়। পূর্ব ভারতের উৎকল, মগধ হতে সর্বপশ্চিমে গান্ধার পর্যন্ত ছড়িয়ে পরে। এক সময় গান্ধার (বর্তমান আফগানিস্তান) হয়ে ওঠে সঙ্গীত ও স্থাপত্য ও চারুকলার প্রাণকেন্দ্র আজকে যা ভাবলেই কেমন বিস্মিত হতে হচ্ছে আমাদের!
যেহেতু অভিনয়ের নিমিত্তে ও যুগপৎ উপস্থাপনের জন্য এই সঙ্গীতের সৃষ্টি তাই বর্তমান ‘প্রবন্ধ গীতি’ এর প্রাথমিক উৎস ধরে নিতে পারি একে। গান্ধর্বগানের সাহিত্য ছিল। আধুনিক কালের কাব্যগীতি বা নাট্যগীতির মতনই। এর মধ্যে মধ্যে ধ্রুবাসঙ্গীত নামক প্রকারের উল্লেখ আছে যার প্রকৃতি ধ্রুবপদ-ধর্মী। ধ্রুপদ যে ধ্রুবপদের অপভ্রংশ তা পাঠকদের বলা বাহুল্য। প্রচলিত ছিল অনেক রাগ-রাগিণী। সুনির্দিষ্ট স্বর-মালার নিয়ম কানুন ছিল। শাস্ত্রোক্ত রয়েছে নানাবিধ প্রকরণ যার প্রায় কিছুই এখন বোঝা যায় না আর। পূর্বেই লিখেছি- সঙ্গীত পাঠোদ্ধার করে বুঝে নেবার বিষয় বস্তু নয়। আমরা ইতিহাস ও এর বিবর্তনের ধারা নিয়ে আলোচনা করছি তাই এত কথা। ও গান গাইতে কেমন হয়- তা লিখে আর কি বোঝাই?
যাই হোক, যেহেতু গান্ধর্বসঙ্গীতকেই আধুনিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আকর বলে লিখলাম- সেহেতু একে আরো একটু বর্ধিত কলেবর করার বাসনা রেখে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি।
(লেখক পরিচিতি – মার্গসঙ্গীত শিক্ষার্থী। বাংলা ভক্তিগীতি, বিশেষত শাক্তপদাবলী ও শাক্তধারার সঙ্গীত নিয়ে মননশীল মানুষ। সাহিত্য ও দর্শন অনুরাগী।)


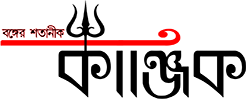


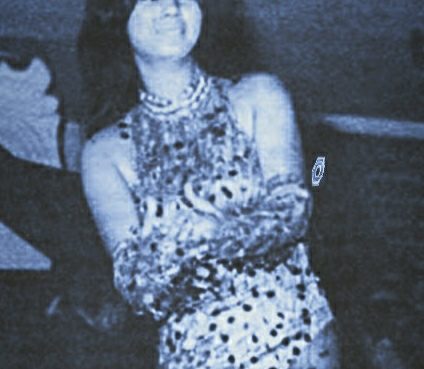

Comment here
You must be logged in to post a comment.