– শ্রী শৈবাল মিত্র
চলতি সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চারু মজুমদারকে স্মরণ করার পাশাপাশি তাদের অনেকে ভোটে অংশ নেয়। পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়। ‘শুয়োরের খোঁয়াড়’ শব্দবন্ধকে আলঙ্কারিকভাবে মেনে নিলেও সংসদীয় পথকে তারা বর্জন করেনি। সংসদীয় কর্মকান্ডে নজর রাখে। চিন্তা আর কাজে, মানুষের এই স্ববিরোধ, ইতিহাসের সব পর্বে থাকে। অতীতে ছিল, এখনও আছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থা শিথিল হলেও, এই ব্যবস্থাকে নাকচ করতে পারে না। চারু মজুমদারের ওপর আস্থা রেখেও তাঁর নির্দেশিত ভোট বয়কটের কর্মসূচিতে সামিল হতে মনের ভেতর থেকে বাধা পায়। পঁচিশ বছর আগে চারু মজুমদারের জীবদ্দশায় যে অবস্থা ছিল, আজও তাই আছে। পরিস্থিতি সামান্য বদলেছে,
বিপ্লবের স্বপ্ন ফিকে হয়ে গেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের রমরমা বেড়েছে। তবে দুটোই আছে। ক্ষীণ স্বপ্ন আর সতেক বাস্তব, দুটো পাশাপাশি আছে। আধুনিকতম কৃৎকৌশলের সঙ্গে মানানসই বিপ্লবী তত্ত্ব ও কর্মসূচি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি বদলাবে না। চারু মজুমদার বেঁচে থাকলে যুগোপযোগী তত্ত্ব, কর্মসূচি হয়তো নিতে পারবেন। তা হবার নয়। আর একজন চারু মজুমদারের জন্যে তাই অপেক্ষা করতে হবে।
চারু মজুমদার থেকে সি এম –
সত্ত্বর দশকে চারু মজুমদারকে টানে সহকর্মীরা সি এম বলে উল্লেখ করতেন। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে, নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুথানের পরে, বছর না ঘুরতে চারু মজুমদার সি এম হয়ে গেলেন। তাঁর নতুন পরিচয় খুব বেশি পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই পুলিশ হেপাজতে চারু মজুমদারের মৃত্যু হয়। চারু মজুমদার থেকে সি এম-এ উত্তরণ, একটি স্বপ্নের জন্ম ও বিনাশের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। কী ছিল সেই স্বপ্ন? স্বপ্ন কি চিরতরে বিনষ্ট হয়? সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে স্বপ্ননির্মাতাকে নিয়ে দুচার কথা বলা দরকার। ১৯১৫ সালে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় তাঁর জন্ম হয়। লেখাপড়া করেছেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল এবং পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। ছাত্রজীবন থেকে বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রথম গ্রেপ্তার হন ১৯৪২ সালে। কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পরে ১৯৪৯-এ দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন। বন্দিত্ব ঘুচলে, ১৯৫২ থেকে তরাই অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ শুরু করেন। চা-বাগিচা শ্রমিকদের আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের পরে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চলে আসেন। সবচেয়ে আকৃষ্ট করেন সেই সময়ের তরুণদের। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল যুবক এবং ছাত্র। সাধারণভাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে তাঁদের চিহ্নিত করা হয়। অধ্যাপক আর বি-র পুরো নাম যে রথীন ব্যানার্জী অএঙ্ক ছাত্রছাত্রী জানে না। তারা আর বি-কে চেনে। সংক্ষিপ্ত নামে অধ্যাপককে ছাত্রছাত্রীরা চিনে নেয়। চারু মজুমদারের নামের আদ্যাক্ষর জুড়ে যারা সিএম করেছিল, তাদের বেশিরভাগ ছিল ছাত্র। শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনেই কর্মীরা তাঁর চারুবাবু বলে উল্লেখ করতেন। চারু মজুমদারের সঙ্গে তাঁর তরুণ অনুগামীদের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বি টি রণদিভেকে বি টি আর, প্রমোদ দাশগুপ্তকে পি ডি জি বলা তরুণরা চালু করেছিল। নেতার মধ্যে ছাত্ররা আদর্শ শিক্ষক খুঁজে বেড়ায়। প্রিয় শিক্ষকের মধ্যে আদর্শ নেতাকে আবিষ্কার করে। সূর্য সেন এভাবে মাস্টারদা হয়ে ওঠেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মাও যে দং বলেন, চীনের মানুষের মনে শিক্ষক হিসেবে আমি বেঁচে থাকতে চাই।
সত্তর দশকের মাঝামাঝি জয়প্রকাশ নারায়ণকে তাঁর তরুণ অনুগামীরা যে পি বলতে শুরু করেছিল। তাঁকেও তরুণরা আদর্শ শিক্ষক ভাবত। অনুসরণযোগ্য মনে করত। শিক্ষণীয় আদর্শ এবং অনুসরণযোগ্য আদর্শের মধ্যে তফাৎ আছে। অনুসরণজয আদর্শ হল উদ্দীপ্ত আলোর মত। তা শুধু শেখায় না, কাছে টানে। সেই আদর্শে মৌলিকতা থাকে। শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে প্রেরণা জোগায়। অনুসরণ করার মতো আদর্শ আর শিক্ষণীয় আদর্শের মধ্যে ফারাকটা তরুণরা ভালো বোঝে। সব শিক্ষককে তারা যেমন অনুসরণযোগ্য মনে করে না, তেমনি সব শিক্ষককে নেতা ভাবে না। রাজনৈতিক নেতাকে শিক্ষকের মর্যাদা পেতে হলে তাঁকে শুধু নেতা হলে চলবে না, দার্শনিক হতে হবে। ‘পলিটিক্যাল লিডার’ থেকে ‘সোশ্যাল ফিলোজফার’ স্টোরে পৌঁছতে হবে। কয়েক হাজার নেতার মধ্যে দু-একজন শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন। শিক্ষকরা নেতা হতে চান না। শিক্ষকের ঘাড়ে ঘটনাচক্রে নেতৃত্ব বর্তালে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ঘটে। তার মানে এই নয় যে, তিনি শিক্ষক নন। সব বিপর্যয় সত্ত্বেও তিনি শিক্ষক এবং ফিলোজফার। তাঁর ‘ফিলোজফি’ বা তত্ত্বচিন্তা ভুল হতে পারে, তার যথাযথতা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু তা যে এক সুনির্দিষ্ট দর্শন, অস্বীকার করার উপায় থাকে না। একজন দার্শনিক শিক্ষক, নেতা হিসেবে ব্যর্থ হতে পারেন, কিন্তু একজন ব্যর্থ নেতার কিছুই হওয়ার নেই।

সি এম-এর দর্শন –
জীবনের শেষ পাঁচ বছরে মজুমদার এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন উপস্থিত করেছিলেন। দর্শনটি হল, বলপ্রয়োগ না করে বিপ্লব করা যাবে না। বিপ্লব এখনই শুরু করতে হবে। অস্ত্রশস্ত্র যা আছে, কাস্তে, কাটারি, দা, কুঠার নিয়ে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে হবে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশে তাঁর দলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম হবে এবং সত্তর দশকের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে দেশের মুক্তি ঘটবে।
খুবই সরল দর্শন। সর্বকালে, সব দেশে বিপ্লবীরা এই কথাগুলো নানা ভাষায় বলে এসেছে। সেই এম-ও বললেন। অন্যদের সঙ্গে তাঁর বলার পার্থক্যটা হল, সরল কথাটা অতীব সহজ ভাষায় বললেন। সহজ করে বলার মত নেতা কজন মেলে? ভাষার হেরফেরে বিপ্লবী নির্দেশ পড়ে যেখানে মনে হয়, বিপ্লব বন্ধ রাখার নোটিস জারি হয়েছে, সেখানে চারু মজুমদারের নির্দেশ বুঝতে কারও অসুবিধে হয়নি। তাঁর ভাষার মধ্যে মারপ্যাঁচ ছিল না। গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুরদের তিনি জোতদারের গলা কাটার আহ্বান জানালেন, ছাত্র-যুবকদের বললেন, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাঁর কথনভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, যা জয়ের অনিবার্যতা সম্পর্কে অনুগামীদের সুনিশ্চিত করেছিল। অনুগামীদের মধ্যে তাঁর সমবয়সী বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন তরুণরা। তরুণরা ছিল অনুগামীদের আশি ভাগ। বিলেত, আমেরিকাবাসী, ভারতীয় অধ্যাপক, বিজ্ঞানীরা কলকাতায় এসে তাঁর কথা শুনে ষোল আনা আশ্বস্ত হতেন। সত্তর দশকের মধ্যে ভারতীয় বিপ্লব জনযুক্ত হবে, এই বিশ্বাসে বিদেশ থেকে সহযোগিতা করতেন। বিশ্বাস করা মহৎ গুণ, আবার অন্ধের মতো বিশ্বাস করা এক ধরনের দায়িত্বহীনতা। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ভাঙচুর ঘটে গেলে, তার দায়িত্ব শুধু বিশ্বাসকারীর ঘাড়ে চাপে না, যারা বিশ্বাস করেছিলেন তাদের ওপরেও বর্তায়। শহর, গ্রামের শিক্ষিত, বঞ্চিত নানা বয়সী মানুষের যে বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন, সেই বিশ্বাসকে নিজের বুদ্ধিমত বাস্তব ভিতের ওপর দাঁড় করাতে কসুর করেননি। বিপ্লব যেহেতু শ্রেণিযুদ্ধ, তাই যুদ্ধকালীন আবহাওয়া তৈরিতে সচেষ্ট হয়ে ছিলেন।
শ্রেণিশত্রুর রক্তে হাত রাঙানোর ডাক তিনিই দিতে পারেন। হাত রাঙাতে গেলে বিপ্লবীকে প্রাণ দিতে হয়, এ তথ্য তাঁর অজানা ছিল না। রক্ত দেওয়া মানে প্রাণ দেওয়া। মৃত্যর জন্য তৈরী থাকতে হবে। চাই আত্মত্যাগ। তরুণরা সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগী হয়। সি এম-এর আত্মত্যাগের তত্ত্ব তরুণ সম্প্রদায় শিরোধার্য করে নিয়েছিল।
কারণে অকারণে অগ্নিভূখ পতঙ্গের মত শত শত তরুণকে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে দেশের মানুষ অবাক হয়েছিল, শিহরিত আতঙ্কিত হয়েছিল। কেউ ভেবেছিল, এই আত্মত্যাগ নবযুগ আনবে, কেউ ভেবেছিল তারুণ্যের অপচয়। যে যাই ভাবক, সি এম-এর দর্শন দাবানলের মত বাপন্থীদের একাংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। দর্শনের দুটি মূল উপাদান ছিল, স্বপ্ন এবং মৃত্যু। স্বপ্নকে মৃত্যুর রঙে সি এম রাঙিয়ে তুলেছিলেন এবং তুলির নিপুণ আঁচড়ে মৃত্যুকে স্বপ্নের মত শিল্পসুষমা দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা যেত, সুনিশ্চিত পা ফেলে মৃত্যুর দিকে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তিনি নিজেও সেকথা জানতেন। তাঁর তীব্র দৃষ্টিতে বেপরোয়া হাবভাব, কথাবার্তায় বিপ্লবের দীপ্তি আর মৃত্যুর বিভা যুগপৎ ঝলসে উঠত। নিজের রোগশীর্ণ শরীর থেকে তিনি মৃত্যর গন্ধ পেতেন, এবং বিপ্লবী ধমক দিয়ে কিছু সময়ের জন্য মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁর বিপ্লবী আবেগে মিশেছিল মৃত্যুচিন্তার চোরা স্রোত। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বারবার আশাভঙ্গের বেদনা এবং নতুন পৃথিবী দেখার ব্যাকুলতা থেকে তাঁর চিন্তায় ভিন্নমুখী দুই প্রবণতা তৈরী হয়েছিল। যে কোনওভাবে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছনো তাঁর দর্শনের মূল কথা। দরকার হলে প্রাণ দিতে হবে, এবং প্রাণ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাজনীতির রহস্যময় মোড়কে মৃত্যুকে গোলাপ ফুলের তোড়ার মত যুব-ছাত্রদের তিনি উপহার দিলেন। আত্মত্যাগ আর আত্মরক্ষার রোমাঞ্চকর ব্যাখ্যা শোনালেন। মৃত্যু ঘিরে এমন এক মনমোহিনী বলয় তৈরী করলেন, যার আকর্ষণে তরুণরা দলবেঁধে জীবন দিতে এল। সামাজিক শক্তি হিসেবে ছাত্র-যুবকদের গুরুত্ব তিনি জানতেন। তাদের উদ্বীপ্ত করার মত আবেগ তাঁর ছিল। সময় এবং পরিস্থতি সাহায্য করেছিল তাঁকে। তাঁর নাতিদীর্ঘ নিবন্ধগুলির বড় অংশ তরুণদের জন্যে লেখা। শ্রমিক, কৃষক এবং বিবিধ বিষয়ে লেখা রচনাতেও ছাত্র-যুবকদের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নতুন পৃথিবী নির্মাণের ঘোষণা বারবার করেছেন। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক প্রতিটি ঘোষণার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তাঁর দর্শন। দর্শনের ভেতরকার স্বপ্নের অংশ বুঝতে অসুবিধে হয় না। স্বপ্ন হল, ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন করা। এই সূত্রে এসেছে মৃত্যুপ্রসঙ্গ। প্রশ্ন আর মৃত্যু গায়ে গায়ে লেগে থাকলেও প্রথমটা সহজে বোঝা যায়। দ্বিতীয়টা বুঝতে সময় লাগে।
মৃত্যুপ্রসঙ্গ এসেছে অন্যভাবে। তিনি যখন বলেন, ‘এটা আত্মরক্ষার যুগ নয়, আত্মহত্যার যুগ’, তখন আত্মরক্ষার অর্থ ‘আপন প্রাণ বাঁচা’ র মত হালকা মনে হয়। আত্মরক্ষার জন্যেই যে আত্মত্যাগ করতে হয়, এ সত্য ধরা পড়ে না। আত্মরক্ষার অর্থ দাঁড়ায় স্বার্থপরতা। আত্মরক্ষার সামাজিক তাৎপর্য অনুক্ত থেকে যায়। তাই হয়েছিল। মুছে গিয়েছিল আত্মত্যাগ আর আত্মবিনাশের সীমারেখা, দুই-এর বিরোধ আর ঐক্য। আত্মরক্ষার চিন্তাবিবর্জিত আত্মত্যাগ যে আত্মহত্যার নামান্তর, এ কথা বলার মত কেউ ছিল না। বললেও শোনা যায়নি। শোনার মত পরিবেশ ছিল না। বাতাসে ঝনঝন করে বেজে চলেছে একটি শব্দ – ‘আত্মত্যাগ’ । আগে কে প্রাণ দেবে তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ‘কে প্রকৃত কম্যুনিস্ট? যিনি জনগণের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারেন এবং আত্মত্যাগ কোন বিনিময়ের প্রত্যাশা করে নয়। দুটো পথ, হয় আত্মত্যাগ নয় আত্মস্বার্থ। মাঝামাঝি কোন রাস্তা নেই।’ (প্রকৃত কম্যুনিস্ট হওয়ার তাৎপর্য কী, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা: ৫৯) ‘আত্মত্যাগে’র বিপরীতে ‘আত্মরক্ষা’র বদলে সি এম ব্যবহার করেছেন ‘আত্মস্বার্থ’ । পারিবারিক, সামাজিক স্বার্থেও যে মানুষ ‘আত্মরক্ষা’ করে, এবং সেটাই মানব সভ্যতার মূল ধারা, এ কথা ভুলে চলবে কেন? সি এমও ভোলেননি। শিলিগুড়িতে ছেড়ে আসা লীগের অভিভাবকহীন সংসারের কথা ভেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উতলা হতেন। তবে সংসারের চেয়ে অনেক বেশি বিভোর ছিলেন সমাজ রূপান্তরের স্বপ্ন আর মৃত্যু নিয়ে। দুটোই তাঁকে বুঁদ করে রেখেছিল। ঘটনা অনেকটা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাবাবিষ্ট হওয়ার মত। রামকৃষ্ণদেবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল কিনা জানা না গেলেও, সি এম হেঁটেছিলেন বারুদ বিছানো পথে। সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং নিজের শরীরের নিরাময়হীন ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, ‘এই সংগ্রামে আমার কি হবে? আমি কী চাই? আমি কি এই মুহূর্তে জনস্বার্থে মরতে রাজি আছি?’ (চেয়ারম্যানের তিনটে লেখা, রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা: ৪০) প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন, ‘জনতার স্বার্থে মরাটাই একটা মানুষের সবচেয়ে মহৎ দায়িত্ব।’
তরুণদের জন্য লেখা হলেও রচনাটিতে সিএম নিজে ঢুকে পড়েছেন। আত্মসমীক্ষা করেছেন। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তরুণ অনুগামীরা। তাদের উদ্দেশে লিখছেন, “ভারতবর্ষের শত সহস্র শহীদ আজ আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁদের কাছে। আজ দিন এসেছে ঋণ শোধ করার।” (ছাত্র যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান, রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা: ৬৯) আঠার থেকে পঁচিশ বছরের তরুণদের কাছে শহীদ হওয়ার জন্যে ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, ভগৎ সিংরা যদি ডাক পাঠায় তরুণদের ঠেকাবে কে? তবে অগ্রজ শহীদদের ডাক পরের প্রজন্মের তরুণদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাঠাতে হবে। সি এম সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে তরুণদের আত্মত্যাগের আবেগ একাকার হয়ে গিয়েছিল। শুধু তরুণ কেন, প্রবীণ, প্রৌঢ়রা পর্যন্ত তাঁর বিপ্লবী আবেগে ভেসে গেলেন। ময়দানে পাওয়া গেল তাঁর অনুগামী কবি, সাংবাদিক সরোজ দত্তের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ। অজ্ঞাতকুলশীলের মত মারা গেলেন কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিক সুশীতল রায়চৌধুরী। দুজনেই তখন মধ্যপঞ্চাশে পৌঁছেছেন। সেই এম-এর রচনায় আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান, আত্মবিসর্জন, জীবন, উৎসর্গ, আত্মাহুতি, রক্তের ঋণ ইত্যাদি শব্দগুলির ক্রমাগত প্রয়োগ পঞ্চাশোত্তীর্ণদেরও বয়সের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তরুণদের চেয়ে তাঁরা তরুণ হয়ে গিয়েছিলেন। যে বয়সে মধ্যবিত্ত সংসারী একজন মানুষ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, বিয়ে-থা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, রাজনীতিতে যুক্ত থাকলে বিধায়ক, সাংসদ হওয়ার ছক কষে, সেই বয়সে পৌঁছে সি এম বন্দুক ধরতে বললেন। শুধু বললেন না, যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়ালেন। তিনি জানতেন, বন্দুক চকোলেট, লজেন্স, সিগারেট, বিড়ি নয়, লেখার কলম, অন্ধের পথ চলার ছড়ি নয়, বন্দুক একবার ধরলে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত নামানো যায় না। জীবদ্দশায় বিপ্লব দেখার সুযোগ যদি না হয়, মৃত্যুর সঙ্গে অবশ্যই দেখা যাবে। যুদ্ধ ঘোষণা করলে জয় অথবা মৃত্যু, কোনও একটা ফয়সালায় পৌঁছতে হয়। সি এম-এর কাছে দুটোই সমান জয়সূচক মনে হয়েছিল। তিনি জানতেন, মৃত্যুকে বাদ দিয়ে বিজয়ের ইতিহাস লেখা যায় না।
(প্রচ্ছদ : ৬০-এর দশকের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের এক দৃশ্য – কলকাতা মহানগরীতে)
(ক্রমশঃ)





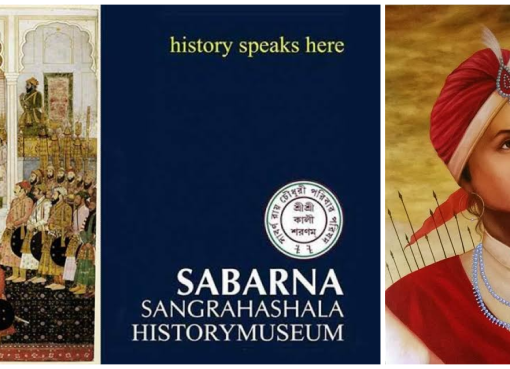
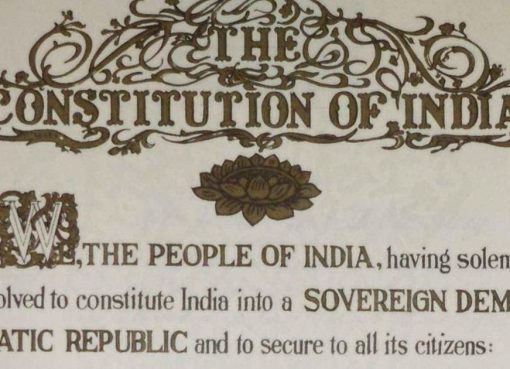
[…] (পূর্ব অংশের পর) […]